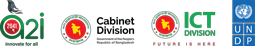-
Upazila introduction
Upazila introduction
History and tradition of the upazila
Geographical and economic conditions
Local people\'s representatives
-
Upazila Parishad
The current council
Functions of Upazila Parishad
development activities-1
-
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উপজেলা পরিষদের মাসিক সভাসমূহের কার্যবিবরণী
-
Minutes of monthly meetings of Upazila Parishad for the fiscal year 2021-2022
-
2021-2022 financial year 17 upazila committee related meeting minutes
-
Annual budget for the fiscal year 2022-2023.
-
five year plan
-
Annual Development Plan for the financial year 2022-2023.
-
Annual Development Program (ADP) implementation progress report for fiscal year 2021-2022.
-
Annual Financial Statement of Upazila Parishad for the financial year 2020-2021
Development activities-2
-
Minutes of monthly meetings of Upazila Parishad for the fiscal year 2024-2025
-
Annual budget for the fiscal year 2024-2025.
-
Minutes of monthly meetings of Upazila Parishad for the fiscal year 2023-2024
-
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট।
-
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।
-
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।
-
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।
-
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উপজেলা পরিষদের মাসিক সভাসমূহের কার্যবিবরণী
-
Upazila administration
Activities of the Executive Officer
UNO\'s office
Laws / Policies
-
Land matters
Demand for land development tax
Land Guard Guard File
Regarding shelter / accommodation
-
List of landless and homeless beneficiaries of the houses allotted in the 3rd phase on the occasion of Mujib Year i.e. A-class rehabilitated families
-
List of beneficiaries related to construction of houses on their own land for those who have land and no house in 2017-2018 financial year.
-
Beneficiary information related to rehabilitation through construction of single house in 2019-2020 financial year.
-
List of homeless families for the financial year 2020-2021.
-
Housing Policy-2020
List A and B of Landless and Homeless Families (2020-2021)
-
List of landless and homeless beneficiaries of the houses allotted in the 3rd phase on the occasion of Mujib Year i.e. A-class rehabilitated families
-
Municipality
Sherpur Municipality Office
Administrator's office
Important information
-
Government office
Matters of law and order and security
Human resource development issues
Health and environmental issues
Agriculture, fisheries, animal and food matters
Land and revenue matters
Education and culture
Engineering and information and communication technology
-
Other institutions
Educational Institutions
- Various projects
-
Download
Important correspondence
-
Cold storage list
-
Different types of application forms
-
List of butchers\' names
-
List of marriage and divorce registrars
-
Information on sawmill installation, license management
-
List of all mosques in the upazila
-
List of names of drug addicts and gamblers.
-
List of food-friendly program dealers and tag officers
-
List of contracted millers under the food-friendly program.
-
List of sacrificial animal skins traders.
-
List of various traders located in Sherpur
-
List of upcoming Durga Puja mandapas in 2020.
-
Recruitment of VGF and VGD Program Tag Officers.
-
List of BADC seed potato sellers
-
Regarding not taking any action regarding the certificate issued by Bangladesh Muktijoddha Welfare Trust.
-
Name of a small ethnic group
-
List of unlicensed pharmacist drug stores / pharmacies.
-
List of Sherpur Upazila Autotempu and Autorickshaw Owners and Battery Powered Easy Bike Owners Association.
-
Cold storage list
-
ICT services
Upazila ICT Branch
-
Minutes of Upazila Innovation Team Meeting
-
Projects by the Innovation Team
-
Annual work plan of the innovation team
-
Innovation Team
-
Database of those who teach marriage without a marriage registrar
-
Imam Portal
-
List of registered Imams
-
The main website of the Info-Government project
-
Upazila ICT Committee
-
Communication
Digital centers and activities
National e-service
-
Minutes of Upazila Innovation Team Meeting
- Tender
- সম্পদ বিবরণের হিসাব সংক্রান্ত
- Regarding public pension
- Communication
-
Upazila introduction
Upazila introduction
History and tradition of the upazila
Geographical and economic conditions
Local people\'s representatives
-
Upazila Parishad
The current council
Functions of Upazila Parishad
development activities-1
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উপজেলা পরিষদের মাসিক সভাসমূহের কার্যবিবরণী
- Minutes of monthly meetings of Upazila Parishad for the fiscal year 2021-2022
- 2021-2022 financial year 17 upazila committee related meeting minutes
- Annual budget for the fiscal year 2022-2023.
- five year plan
- Annual Development Plan for the financial year 2022-2023.
- Annual Development Program (ADP) implementation progress report for fiscal year 2021-2022.
- Annual Financial Statement of Upazila Parishad for the financial year 2020-2021
Development activities-2
- Minutes of monthly meetings of Upazila Parishad for the fiscal year 2024-2025
- Annual budget for the fiscal year 2024-2025.
- Minutes of monthly meetings of Upazila Parishad for the fiscal year 2023-2024
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।
-
Upazila administration
Activities of the Executive Officer
UNO\'s office
Laws / Policies
-
Land matters
Demand for land development tax
Land Guard Guard File
Regarding shelter / accommodation
- List of landless and homeless beneficiaries of the houses allotted in the 3rd phase on the occasion of Mujib Year i.e. A-class rehabilitated families
- List of beneficiaries related to construction of houses on their own land for those who have land and no house in 2017-2018 financial year.
- Beneficiary information related to rehabilitation through construction of single house in 2019-2020 financial year.
- List of homeless families for the financial year 2020-2021.
- Housing Policy-2020
List A and B of Landless and Homeless Families (2020-2021)
-
Municipality
Sherpur Municipality Office
Administrator's office
Important information
-
Government office
Matters of law and order and security
Human resource development issues
Health and environmental issues
Agriculture, fisheries, animal and food matters
Land and revenue matters
Education and culture
Engineering and information and communication technology
-
Other institutions
Educational Institutions
-
Various projects
Projects implemented by Upazila Engineer
Projects of Upazila Project Implementation Office
Other projects
-
Download
Important correspondence
- Cold storage list
- Different types of application forms
- List of butchers\' names
- List of marriage and divorce registrars
- Information on sawmill installation, license management
- List of all mosques in the upazila
- List of names of drug addicts and gamblers.
- List of food-friendly program dealers and tag officers
- List of contracted millers under the food-friendly program.
- List of sacrificial animal skins traders.
- List of various traders located in Sherpur
- List of upcoming Durga Puja mandapas in 2020.
- Recruitment of VGF and VGD Program Tag Officers.
- List of BADC seed potato sellers
- Regarding not taking any action regarding the certificate issued by Bangladesh Muktijoddha Welfare Trust.
- Name of a small ethnic group
- List of unlicensed pharmacist drug stores / pharmacies.
- List of Sherpur Upazila Autotempu and Autorickshaw Owners and Battery Powered Easy Bike Owners Association.
-
ICT services
Upazila ICT Branch
- Minutes of Upazila Innovation Team Meeting
- Projects by the Innovation Team
- Annual work plan of the innovation team
- Innovation Team
- Database of those who teach marriage without a marriage registrar
- Imam Portal
- List of registered Imams
- The main website of the Info-Government project
- Upazila ICT Committee
- Communication
Digital centers and activities
National e-service
-
Tender
Notifications
All notices
-
সম্পদ বিবরণের হিসাব সংক্রান্ত
সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সম্পদের হিসাব বিবরণী ফরম
-
Regarding public pension
Information on Public Pension Scheme
-
Communication
Helpline
Office location
Facebook page
শেরপুরের ইতিহাস
শেরপুর একটি নাম, একটি অতীত চিত্রের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ও সর্বোপরি ইহা এক মহাকালজয়ী ঐতিহাসিক প্রাচীন অধ্যায়। ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এ নামটি কেবল বগুড়া জেলার অত্র স্থানেই সীমাবদ্ধ নহে বরং এছাড়া ও এ নামটির মাহাত্ন্য ও ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায় কাশ্মির, আফগানিস্তান, ভারতের বীরভূম ও বাংলাদেশের সিলেট ও ময়মনশাহী জেলাতে। যে মহান ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, শেরপুর নামের উদ্ভব হয়েছিল, সম্ভবতঃ তিনি হলেন আফগান বালক ফরিদখান । এ বালক বীর পরবর্তীকালে নরখাদক এক বিশালকায় হিংস্র ব্যাঘ্র হত্যা করে, শেরখান নামে অভিহিত হন। তাঁরই নামানুসারে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য স্থানকে ঐতিহাসিক ভাষায় পরিচিহ্নিত করেন, বগুড়া জেলার শেরপুর তম্মধ্যে অন্যতম। শেরপুর একটি প্রাচীন নাম । এ নামটি আজ হতে প্রায় চারশ বছর পূর্বে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করে থাকবে। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চিন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েস্থ সাং প্রাচীন পৌন্ড্রবর্দ্ধনে কালাতো (Kalato) নামে একটি সুবিশাল নদী অতিক্রম করে আসাম রাজ্যে প্রবেশ করেন বলে জানা যায়। হিউয়েস্থ সাংঘ কর্তৃক উল্লেখিত সেই নদীটিই যে আজকের করতোয়া এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।
পুরাতন তন্ত্রাদি সূত্রে জানা যায় যে এক সময় করতোয়া নদীদ্বারা বঙ্গ ও আসাম (কাররুপ) পৃথকৃত ছিল। কাজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন বৌদ্ধ আমল হতেই শেরপুরের ঐতিহাসিক পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।
দিল্লীর সুলতানী আমলে বগুড়া তথা গোটা উত্তর বঙ্গ অনেক বারই সুলতানদের কবলিত হয়েছিল। অভিযান কালে কেউ কেউ শেরপুর ও মহাস্থানকে উপ রাজধানী ও সেনা ছাউনী রূপে ব্যবহার করেছেন। আসাম ও কোচ বিহার অভিযান কালে এ স্থানটি এক শক্তিশালী ঘাটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো । কথিত আছে যে আসাম আক্রমণ কালে সেনাপতি মীর মুমলা (১৬৬১) বেশ কিছুদিন শেরপুর ও ভবানীপুরে বিশ্রাম গ্রহন করেন।
আজকের শেরপুর, এক মহানগরীর স্মৃতি বিজড়িত একটি পরিত্যক্ত খন্ড উপশহর মাত্র। পূর্বে এটি ছিল ধনে জনে পরিপূর্ণ এক বিশাল নগরী। অতীতে এ জনপদের প্রশংসায় মুখরিত ছিল সারাটি গাংগের (সাবেক বাংলা) সমগ্র বঙ্গ ভূমি। এ নগরীর খোশ নাম ছড়িয়ে পড়েছিল পাক-ভারত বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতের মালয়ে, সুমাত্রায় জাভায়, ব্রক্ষদেশ শ্যাম আর সিংহলের মত দূর দুরান্তরের দেশে, এমনকি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তেও শেরপুরের পাশ দিয়ে বয়ে চলছে আজকের ক্ষীণ স্রোতা করতোয়া, কিন্তু আদিতে ছিল এটি করস্রোতা। কথিত আছে যে অধুনা বারদুয়ারী ঘাট এককালে আন্তর্জাতিক মহানদী বন্দর রূপে বিবেচিত হতো। সেকালে এ নদীটির বিস্তৃতি ছিল এখান হতে মেহমানশাহীর শেরপুর পর্যন্ত প্রসারিত। এ নদী দিয়ে বাণিজ্য তরী মালায় সিংহল, সুমাত্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো । তেমনি এর বিশাল ঘাটে এসে ভিড়তো ভিন দেশের রকমারি বাণিজ্য তরী।
অধুনা উত্তর বঙ্গ আদিকাল হতে আদি শূরের আমল পর্যন্ত পৌন্ড্রবর্দ্ধন নামেই পরিচি ত ছিল। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে আদিশূর জয়ন্ত যখন, পঞ্চ গৌড়ের অধিশ্বর হন, তখন হতে পৌন্ড্রদের পরিবর্তে গৌড় দেশ নামে অভিহিত হয়। কিন্তু রাজধানী পৌন্ড্রবর্দ্ধনেই থেকে যায়। অতঃপর তদ্বংশীয় রাজা প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর যখন একই সময়ে রাজত্ব লাভ করেন, তখন গৌড়দেশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বরেন্দ্র শূরের অধিকৃত খন্ডের নামকরন হয়, বরেন্দ্র দেশ এবং এই অংশেই আমাদের আলোচ্য শেরপুর অবস্থিত।
শেরপুর নাম করনের পেছনে রয়েছে মজবুত ঐতিহাসিক ভিত্তি। বাস্তবে নামকরণ অপেক্ষা ইহার ঐতিহ্যই যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং সুপ্রাচীন এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই প্রাচীনত্বটি খূজে বেরকরা কেবল দুঃসাধ্যই নয়, বরং রীতমত এক অসম্ভব ব্যাপার । অধুনা শেরপুর অপেক্ষা প্রাগৈতিহাসিক শেরপুর ছিল সর্বাধিক সুপ্রসিদ্ধ। নাম করনের পূর্বেও এ স্থানটি তার নিজস্ব মহিমায় ছিলমূর্তমান। প্রাগৈতিহাসিক এই স্থানটির ভিন্ন কোন কোন নাম ছিল কি-না, তা বলা কঠিন । তবে সেই অজ্ঞাত যুগে যদি স্থানটি উত্তর বঙ্গের প্রবেশদ্বার অথবা বরেন্দ্র তিলক নামে অভিহিত করা হতো, তবে মোটেই বেমানান হতোনা নিশ্চয়।
শেরপুর নামটিই এর সঠিক ঐতিহ্যের অন্যতম প্রকাশক। এ নামটি অবিতর্কিত হলেও এ সম্পর্কে অল্প বিস্তর আলোচনা ও পর্যালোচনা অবকাশ আছে বই কী ? আমাদের এই উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য অনেক ক’টি স্থানই শেরপুর নামে ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে বহুযুগে পূর্বে । অন্যত্র যে কারনেই হোক, তবে উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক শেরপুর নগর যে সম্রাট শেরশাহের নামেই পরিচিহ্নিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। আমরা জানিযে, পাঠান নৃপতি শেরশাহ শূরী ছিলেন এক অবিসংবাদিত ও পরম জনপ্রিয় সম্রাট । বাংলার জনগণ তাঁর প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। সীমিত সময়ের মধ্যে তিনি এখানকার জনগনের কল্যানার্থ অনেক অনেক উল্লেযোগ্য কাজ করেন। এজন্যই তার সুনামের নজরানা হিসেবে বগুড়া জেলায় এ স্থানটি শেরপুর নামে পরিচিহ্নিত হয়েছে। তদানীন্তন বাংলার পূর্তগীজ গভর্নর ভনডেন ব্রুক কর্তৃক বিরচিত বঙ্গ ভূমির মানচিত্রে, তিনি শেরপুরকে Ceerpoor Mirt অর্থাৎ Sherpur Murcha নামে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া সমসাময়িক অপরাপর ঐতিহাসিকগন ও এ স্থানটিকে শেরপুর নামেই উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ ১৫৪০-১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় এ স্থানটির নাম করণ হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, শেরশাহ অথবা তাঁর কোন সেনাপতি এই নামটি প্রবর্তন করে থাকবেন । কেউ কেউ অনুমান করেনযে ‘সির’শব্দ হতে শেরপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে। মধ্য যুগীয় অনেক গ্রন্থে শেরপুরের স্থলে সেরপুর উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবত তারা ‘সির’ শব্দকেই অনুসরণ করে থাকবেন। কারণ, হয়রত শাহ্ তুরকান শহীদের সির বা মস্তক এখানেই সমাধিস্থ হয়েছে এবং শেরপুরের মুসলীম ইতিহাসে তা যে কোন উল্লেখযোগ্য হলেও আদৌ গ্রহন যোগ্য নয়। কারন, ‘সির’ শব্দটির রূপান্তর সিরমোকাম ও সেরুয়া গ্রামের নামেই সীমাবদ্ধ, এর বাইরে নয়। অন্যকথায় শেরপুর নামের উৎপত্তি অন্য কোন শব্দ হতে হয়নি বরং হয়েছে শেরশাহ্ এবং একমাত্র শেরশাহ্ নাম হতেই।
এ স্থানের অপর দুটি শ্রুত নাম সোণাপুর ও ‘‘বার দুয়ারী’’ লোকমুখে শোনা যায়। কথিত আছে যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তৎকালে নাটোর রাজগণ, তাঁদের সুবিস্তীর্ন জমিদারী গঠন করে তুলেছিলেন এবং তারা এখানে বার দুয়ারী নামে একটি তহসীল কাছারী স্থাপন করে ছিলেন। তাইতো এর অপর নাম বারদুয়ারী শেরপুর। সোণাপুর সম্পর্কে জনশ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বলা হয়ে থাকে যে, সেকালে একবার এখনে প্রচুর স্বর্ণ সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল অথবা এস্তানটি এক সময় প্রাচ্যের স্বর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল। তাই একে সোনাপুর নামে আখ্যায়িত করা হয়। কেহ কেহ ‘‘সোনাভান’’ পুথি কেতাবে উল্লেকিত সোণাপুরকে শেরপুরের আদিনাম বলে কল্পনা করেন। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে শের (ব্যাঘ্র) শব্দ হতে শেরপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে। কারণ এককালে এখানকার জংগলে অসংখ্য ব্যাঘ্র বাস করতো। বস্ত্তুতঃ নাম করনের এসব অবতারণা, কথার কথা বই আর কিছুই নহে।
অধুনা শেরপুর মূল শহরটি প্রাচীন পরিখা বরাবর অবস্তান করছে। অধুনা সির মোকাম হতে শুরু হয়ে নদীর পশ্চিম তীর বরাবর মির্জাপুর পর্যন্ত প্রাচীন সেই মোর্চা বা পরিখাটি প্রলন্বিত ছিল। কথিত আছে যে তদানীন্তন দক্ষিণ বঙ্গের বার ভৌমিকের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, যশোহরের প্রতাপাদিত্য কে শায়েস্তা করনার্থই শেরপুরের উল্লেখিত দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল। তৎকালে, বর্তমান পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অধিকাংশ স্থানই যশোহর জেলার অর্ন্তভূক্ত এবং উহা রাজা প্রতাপাদিত্যের শাসনাধীন ছিল। মূলতঃ রাজাপ্রতাপাদিত্যকে বশীভূত করার জন্যই মুঘল সেনাধ্যক্ষ এখানে আস্তানা গড়ে তুলেছিলন।
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেকালে মেহমান শাহী পরাগণার সদর দপ্তর বা হেড কোয়ার্টাার মোর্চা শেরপুরেই অবস্থিত ছিল। এই শেরপুর মোর্চার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক তুলেছেন, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লেখক, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় । তিনি উল্লেখ করেন’’ আইনে আকবরীর সেরপুর মুর্চা, ময়মনসিংহ, বগুড়া বা মুর্শিদাবাদের সেরপুরের মধ্যে কোন্টি তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়না’’। তিনি শেরপুর মোর্চা কে মুর্শিদাবাদের অর্ন্তভুক্ত করে দেখাতে চান। কিন্তু আইনে আকবরীতে দেখা যায় যে, উহা মেহমানশাহী পরগনায় অবস্থিত এবং বগুড়া জেলার অন্তর্গত । গ্লাড উইন অনুদিত আইনে আকবরীতে লিখিত হয়েছে’’
Mehman shahy, Commonly called sherpur Murcha” অর্থাৎ মেহমান শাহীকে সাধারণ্যে শেরপুর মোর্চা বলা হয়ে থাকে । সুতরাং নিখিল বাবুর অনুমান মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়।
ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে প্রাচীন শেরপুর মোর্চা সেকালে এক মহাসমর ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছিল । এখানে মানসিংহের সহিত দুর্ধষ আফ্গানদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধের বিবরণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ভাষায় নিম্নরুপঃ ‘‘উড়িষ্যা হইতে মোগল দিগকে বিতাড়িত করিয়া আফগানেরা বাঙ্গালা পর্যন্ত ধাবিত হয়। ........... সেই সময় বিশ হাজার আফগান, ওস্মানের পতাকা মূলে সমবেত হইয়াছিল। সেরপুর মুর্চার পশ্চিম প্রান্তরে উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম বধিয়া উঠে । আফগানদিগের সহিত বহু সংখ্যক রনহস্তী ছিল। সর্বাগ্রে সেই সমস্ত মদোন্মত রণহস্তী স্থাপিত হইলে, মোঘল ও রাজাপুতগণ তাহাদের প্রতি গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করায়, হস্তীগণ বিকট আর্তনাদ করিতে করিতে ছত্র ভংগ হইয়া পড়ে এবং আফগানগণও উপর্যু্যপরি আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মোগল ও রাজপুতগণ কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎধাবন করে, তাহারা উড়িষ্যা মুখে অগ্রসর হয়’’। মেরচা শব্দটি শেরপুর নামের বহুল প্রচলিত অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক কালে মোর্চা ব্যতীত শেরপুর নাম অবোধ গম্য ছিল। এই শেরপুরে আমরা আরও তিনটে মোর্চার উল্লেখ দেখতে পাই যথা, গ্রাম মোরচা, বন মোরচা ও পান মোরচা। শেরপুরের দক্ষিণ পূর্বাংশ গ্রাম মোরচা, মধ্যাংশ পান মোরচা ও উত্তর পশ্চিম প্রান্তে বন মোরচা অবস্থিত। শেরপুরের দক্ষিণ ও পূর্বাংশ সৈয়দপুর এবং উত্তর ও পশ্চিমাংশ উলিপুরের অন্তর্গত।
অধুনা শেরপুর শহরটি ধ্বংসাবশেষের অবশিষ্টাংশ মাত্র। এককালে এ শহরটির বিস্তৃতি ছিল দৈর্ঘে ও প্রন্থে যথাক্রমে বার ও ছয় মাইল। প্রাচীন মূল শহরের সর্বাংশই এখন সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মূল শহরটি কিরুপে এবং কখন যে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ সম্পূর্ণরুপে অনুপস্থিত। বিশেষ ভাবে অনুধাবন ও অনুমান করা যায় যে প্রাচীন টোলা, মিঞা টোলা, পাঠান টোলা ও ধড় মোকাম প্রভৃতি এককালে শহরের উল্লেখযোগ্য মহল্লা রূপে পরিগণিত হতো। এখানে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ টোলা মসজিদ খেরুয়া, মসজিদ ও বিবির মসজিদ প্রায় একই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে প্রমান পাওয়া যায়। একই মহল্লায় একাধিক বৃহদাকার মসজিদের অস্তিত্ব দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেকালে এ স্থানটি ছিল মুসলীম জনবহুল এলাকা। অধুনা শেরপুর শহরটি প্রাচীন মূল নগরীর অবিচ্ছেদ্য অংশ কিনা তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ শহরটির প্রাচীনত্ব ও নেহাত কম নয়। সম্ভবতঃ মূল প্রাচীন নগরীর পতনের পর পরই এটি দ্বিতীয় মূল শহর হিসেবে গড়ে উঠে থাকবে। সংগত কারনেই এক সময় শেরপুরকে ‘‘উত্তর বঙ্গের প্রাচীন দিল্লী’’ নামে অভিহিত করা হতো। কারন তখনকার দিনে কেবল শেরপুর, বোয়ালিয়াও ঘোড়াঘাট নামেই উত্তর বংগের অস্তিত্ব বুঝানো হতো। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বপর্যন্ত শেরপুর ও মহাস্তান ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান। লুটেরা দস্যুদের নৈরাজ্য রোধের জন্য তদানীন্তন ইংরেজ বেনিয়া সরকার, বগুড়া নামে আর একটি পৃথক জেলা সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। বলা হয়ে থাকে যে, সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের পুত্র বাংলার শাসন কর্তা নাসির উদ্দিন বগরা খানের নামানুসারেই নবগঠিত এই জেলার নামকরণ হয়েছিল। বগুড়ার পরিবর্তে যদি শেরপুরে জেলা সদর প্রতিষ্ঠা করা হতো, তাহলে ইহার ঐতিহ্য চির কাল অক্ষুন্ন থেকে যেতো বই কী। জেলা গঠনের পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশাসনিক মর্যাদায় শেরপুর দ্বিতীয় স্থানীয় হয়ে পড়ে। মুঘল যুগে শেরপুরছিল সুপ্রসিদ্ধ এক সীমান্ত ঘাটি। ১৭৬৫ ঈসায়ী থেকে মুঘল সম্রাটদের নিকট হতে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনী বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সহ এই অঞ্চল ও করলগত করে ফেলে। উত্ত বঙ্গের অমর প্রতীক হিসেবে শেরপুরের মর্যাদা ছিল সমূন্নত কিন্তু ঢাকায় মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে, ইহার প্রাধান্য বহুলাংশে লোপ পায় । (২) মুঘল আমলে শেরপুর বিদ্রোহীদের এক মহা মিলন কেন্দ্রে প্ররিণত হয়েছিল, কারণ সম্রাট আকবর কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর বিদ্রোহী কাকশাল গোত্রের লোকেরা এখানে শক্তিশালী আস্তানা গড়ে তুলেছিল।
প্রসিদ্ধ টোলা চৌহদ্দির অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে মাটি খনন কালে অনেক প্রাচীন ঘর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। কয়েক স্থানেখনন কালে শেরশাহী আমলের রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। টোলা মহল্লার পুর্বাংশে অবস্থিত হামছায়াপুর গ্রামটি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাচীন বলে অনুমিত হয়। মুঘল আমলে ইহা পাটান টোলা নামে পরিচিত ছিল। সেকালে এখানে সরকারী তহসীল কাছারী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। পরবর্তী কালে প্রলয়ংকরী ভূমিকল্প অথবা অন্য কোন দৈব দুর্যোগে পাঠান টোলার ঘরবাড়ী ধ্বংস প্রাপ্ত হলে স্থানটি গভীর অরণ্যে পরিণত হয়। অতঃপর অরণ্যের কোন কোন অংশে বুনো বা সাঁওতাল শ্রেণীর লোকজন বাস আরম্ভ করে। পরিশেষে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আসাম হতে আগত বাস্তহারাগণ এখানে পুনর্বাসন লাভ করলে, পাঠান টোলারঅরণ্য সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়ে যায়। এখানে চাষাবাদ ও ঘর গৃহ নির্মাণকালে টোলা ও পাঠান টোলার এখানে ওখানে অনেক প্রাচীন কীর্তি যথা, দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ, মৃৎশিল্পের নমুনা, ধনুক যুদ্ধে ব্যবহৃত মৃত্তিকা বর্তুল, তসবি্হ দানা ঘটি বাটি, কড়ি মুদ্রা, বৌদ্ধ মৃর্তি প্রভৃতি বহুল পরিমানে পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবতঃ অধুনা হামছায়াপুর বিশেষতঃ বর্তমান ইতিহাস প্রণেতার বাসভবন সংলগ্ন স্থান সমূহ সেকালে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মহল্লা ছিল বলে মনে হয়। কারণ এ অংশের মৃত্তিকায় প্রাচীন উপাদান এত বেশী অবশিষ্ট রয়েছে যা দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে চাষাবাদ করার পরও দূরীভূত হয়নি। এখানে প্রাপ্ত ছোট বড় মৃত্তিকা বর্তুল দৃষ্টে মনে হয় যেন এক কালে এ স্থানটি কোন সমরক্ষেত্র অথবা অস্ত্র নির্মাণ কারখানা রূপে ব্যবহৃত হতো।
অধুনা শহরটি প্রাচীন শেরপুরের ভাংগা গড়ার পঞ্চম সংস্করণ বটে। ইতোপূর্বে এই শহরটি কমপক্ষে চার বার চুড়ান্ত ধ্বংসাবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে । পরিশেষে আজকের শেরপুর দূর অতীতের স্মৃতি বক্ষে জুড়ে ক্ষুদ্রতম পরিসরে মহাকালের স্বাক্ষররূপে দাঁড়িয়ে আছে।
বৃহত্তর বগুড়ার জয়পুরহাট মহকুমা, অতঃপর জেলা শহরে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত শেরপুর ছিল দ্বিতীয় মর্যাদাশীল এক ঐতিহাসিক শহর। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখনও অনুধাবন যোগ্য। শেরপুর এক সময় দালান বা কোঠা বাড়ীর শহর বলে আখ্যায়িত হতো। জমিদারী আমলে এখানে এত সংখক দ্বিতল, ত্রিতল প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল যে, এগুলি নির্মাণ কল্পে অসংখ্য রাজমিস্ত্রিকে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হতো এবং উক্ত মহল্লাটি পরবর্তী কালে মিস্ত্রি পাড়া নামে অভিহিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ঐ প্রাসাদমালা দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারেনি-কারণ, বঙ্গাব্দ ১২৯২ সালে (৩০শে আষাঢ়, পূর্বাহ্ন ৬ ঘটিকা) সংঘটিত এক সর্বনাশা ভূমিকম্পে এ শহরের বর্ননাতীত ক্ষতি সাধিত হয় এবং এর ফলে জনপদের বিশাল সংখ্যক মানুষ দালান চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে।
ভুমিকম্পের পুর্বে শেরপুর ছিল এক সুশোভিত জন পদ। এই তান্ডব লীলায় যে অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ পেশ করা কঠিন । উক্ত মহাদুর্যোগের ফলে একমাত্র শেরপুর শহরেই ৪৫/৫০ জন লোকের প্রাণ হানি ঘটে। যারা এ সর্বনাশা তান্ডবে নিহত হয়েছেন, তম্মধ্যে মুন্সী বাটির শ্রীযুক্ত রাধা বমন মুনসীর বড়স্ত্রী, চন্দ্র কিশোর মুনসীর চতুর্থ পুত্র, কালি কিশোর মুনশী মহাশয়ের মাতা ও চার সন্তানসহ অত্র পরিবারের নিজস্ব মোট আঠার ও অপরাপর আরও এগার জনের প্রাণ হানি হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে অবস্থিত শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির সহ আরও অনেক গুলি অতি প্রাচীন মন্দির ও দেবালয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।
পুর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে মোরচা শেরপুর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। অনেকে অনুমান করেন যে করতোয়া নদী যখন এখান হতে মেহমানশাহী পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল এবং কামরূপ (আসাম) কে যেকালে করতোয়া নদী দ্বারা বঙ্গ ভুমি হতে বিভক্ত ও পৃথক করা হতো সেই আমলে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেহ কেহ মত পোষন করেন যে, জৌন গনই এখানে সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ ও নগর পত্তন করেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে বৌদ্ধগণই সর্বাগ্রে এ শহরের গোড়া পত্তন করেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগেই করতোয়া এখন হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিস্ত্তৃত ছিল এবং সেই বিশাল নদীটি পার হতে তখন মাথাপিছু খেয়া মাগুল দশকাহন প্রয়োজন হতো । সে আমলের এ বিবরনটুকু ব্যতীত আর কোন তথ্য উদ্ধার করা যায়নি। অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধ শাসনামলের শেষের দিকে বল্লাল সেন তখনকার প্রাচীন কমলাপুর বা রাজবাড়ী মুকুন্দে এক নতুন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সেই সেই রাস্ট্রের সুবিধালাভের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন স্থান হতে হিন্দু প্রজাগণ এখানে এসে বসবাস শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেন বংশের পতনের পর যখন মুসলমান প্রভাব বিস্তার হতে থাকে, তখন হিন্দু গন অধূনা শেরপুরে প্রত্যাবর্তন করে। অধুনা বারদুয়ারী ঘাট তৎকালে আন্তর্জাতিক নদী বন্দর রূপে ব্যবহৃত হতে। বানিজ্যিক সুবিধা ছাড়াও আবাসিক সুযোগ সুবিধায় উৎসাহী লোকেরা সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। ফলে নানা শ্রেণীর লোকজন এখানে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে বসে। লক্ষ্যনীয় যে মোর্চা উত্তর উপ-শহরে এককভাবে হিন্দুগণই অধিবাসী হয়। অথচ তখনকার দিনে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা নেহাত কম ছিলনা। সম্ভবতঃ মুসলমানদের অধিকাংশই তখন কৃষি কাজে লিপ্ত থাকতো হেতু শহরমুখী হতে পছন্দ করতোয়া শহরটি (শেরপুর) বিপুল সংখ্যক হিন্দু পরিবারের বাসস্থল হলেও এর চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকা সমূহ মুসলমানদের পবিত্র স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং এটা মোটেই অমূলক নয় যে, প্রাচীন মোর্চা নগরীর বিস্তৃতি ছিল সুবিশাল এবং এর মুসলিম নাগরিকদের সংখ্যা ছিল বেশুমার।
অধুনা শেরপুর গন্ডির আদি বাসিন্দা কারা, তা সঠিক করে বলা কঠিন । তবে অনেকেই তিলিদেক এখানকার আদি বাসিন্দা বলে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। কারণ, তিলিগন দক্ষ ব্যবসায়ী । তাই এরা বিভিন্ন স্থান হতে এসে অত্র বাণিজ্য কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে বসবাবস আরম্ভ করে। অধুনা শেরপুর এক সময় ছিল মুসলমান শূন্য জনপদ । অন্য কথায় হিন্দুগন এবং তাদের মধ্যে ব্রাক্ষণ, তিনি, সৌগন্ধ বনিক প্রভৃতি গোষ্ঠিই ছিলেন এখানকার দন্ডমুন্ডের অধিকর্তা।
তিলিদের আগমনের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়না। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় যে অপরাপরদের চেয়ে এরা বহুগুণে প্রাচীন বাসিন্দা। এদের আদিত্বের অনুকুলে আরও বলা যেতে পারে যে তিলিদের মধ্যে বড় বাড়ী ছোট বাড়ী ও কুঠি বা কোঠা বাড়ী নামে বহুপ্রাচীন কাল হতেই এরা প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছেন। সুতরাং তিলিরাই যে অধুনা শেরপুরের আদিম বাসিন্দা, তাতে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ থাকেনা। শেরপুরের তিলিরা সাধারনতঃ দু’ মহল্লায় বিভক্ত ছিলেন যথা, দাস পাড়া ও মহাস্তানপট্রি।
শেরপুর ঐতিহ্যবাহি স্থান /স্থাপনা
পাঁচ শতাব্দী প্রচীন শেরপুরের খেরুয়া মসজিদ
সুপ্রাচীন শহর বগুড়ার শেরপুর। বগুড়া পৌরসভার একদিন আগে ১৮৭৬ সালে শেরপুর পৌরসভা স্থাপিত হয়। এখানে রয়েছে অনেক ঐতিহাসক নিদর্শন। খেরুয়া মসজিদের সুনিপুন নির্মান শৈলী এখনও মানুষের মন কাড়ে। শাহতুরকান,শাহবন্দেগীর মাজার এখানে মুসলিম ঐতিহ্যেরই স্বাক্ষী। ইতিহাস খ্যাত অনেক কাহিনী বর্তমান এই প্রর্জন্মের কাছে আজো প্রায় অজানা।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, এখানে ৩৬০ জন আউলিয়া সমাহিত আছেন। তাদের অনেক স্মৃতি কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও এখনো অনেক স্মৃতি চিহৃ বিদ্যমান। ইতিহাস খ্যাত হযরত শাহ তুর্কান ও গাজী শাহ বন্দেগী এর সমাধিস্থান দরগাহ শরীফ আমাদের মাঝে কালের স্বাক্ষী হয়ে আজো বিদ্যমান।
উত্তরাঞ্চলের প্রবেশদ্বার বগুড়ার শেরপুর শহরের অদূরে মাত্র ১ কিলোমিটার দক্ষিন-পশ্চিমে প্রায় সাড়ে৪শ বছরের প্রাচীন খন্দকার টোলা খেরুয়া মসজিদের অবস্থান। গ্রামীণ নিড়িবিলি সবুজ শ্যামল পরিবেশে অপূর্ব নির্মান শৈলী সম্বলীত খেরুয়া এই মসজিদ আজোও দর্শনাথীদের হৃদয় কাড়ে।
মসজিদের গায়ে সংস্থাপিত ফার্সি শিলালিপি থেকে জানা যায়, জওহর আলী কাকশালের পুত্র মির্জা নবাব মুরাদ খানের পৃষ্টপোষকতায় আব্দুস সামাদ ফকির ৯৮৯ হিজরীর ২৬ জিলকদ (১৫৮২ খ্রিঃ) সোমবার মসজিদটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উত্তর দক্ষিন লম্বা মসজিদের বাইরের মাপ দৈর্ঘ্য ৫৭ ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে ২৪ ফুট। আর ভিতরের মাপ দৈর্ঘ্য ৪৫ ফুট ও প্রস্থে সাড়ে ১২ ফুট। চারিদিকের দেওয়াল গুলো প্রায় ৬ ফুট পুরো। মসজিদের চারকোণে ৪টি মিনার ও পূর্ব দেওয়ালে ৩ টি দরজা রয়েছে। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের মাঝের দরজাটি অন্য দুটি থেকে আকারে অনেক বড়। আয়তকার ফ্রেমের মধ্যে অধ্যগোলাকার মেহরাব গুলো স্থাপিত। মসজিদের কার্নিস বাকানো আছে। দেওয়ালে কিছু কিছু পোড়া মাটির চিত্র ফলকও ছিল। তবে সংখ্যায় খুবই, দেওয়ালগুলো সাদাসিধে ধরনের বলা যেতে পারে। বাগেরহাটের ৬০ গম্বুজ মসজিদ ও শাহজাদপুরে অবস্থিত প্রাচীন মসজিদের নির্মান শৈলীর সাথেএই খেরুয়া মসজিদের অনেক মিল দেখা যায়। ইট ও চুন শুড়কী ছাড়া খেরুয়া মসজিদের নির্মান কাজে বৃহদাকার কৃষ্ণ পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের গায়ে দুইটি শিলালিপি ছিল, যার একটির ভিতরে রক্ষিত ছিল মুল্যবান সম্পদ যা পরবর্তীতে ব্যহৃত হয়। আর একটি বর্তমানে পাকিস্থানের করাচি যাদুঘরে রয়েছে। সম্রাট আকবরের আমলে মসজিদটি নির্মিত হওয়ায় এর গাঁয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাতিক্রম অনেক চিহৃ পাওয়া গেছে। স্থাপত্য বিশারদদের মতে খেরুয়া মসজিদে সুলতানী ও মুঘল আমলের মধ্যবর্তী স্থাপত্য নির্দশন প্রকাশ পেয়েছে। এতে বার কোনা ও আট কোনা কলাম ব্যবহার করা হয়েছে। যা বাংলার স্থাপত্য শিল্পে বিরল। এই মসজিদটি বহুদিন অনাদরে পড়ে ছিল। এর মধ্যে অনেক গাছ পালা জন্মে চারিদিকে জঙ্গলে পরিপূর্ন ছিল। ৯০ এর দশকে প্রত্নতত্ত বিভাগ এই মসজিদটি সংস্কার করার ফলে মসজিদের আগের অবস্থা ফিরে এসেছে। এখন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুম্মার নামাজ আদায় করা হয়। প্রত্নতত্ত বিভাগ ১৯৮৮ সাল থেকে মসজিদের ৪৮ শতক জায়গাসহ দেখাশোনার জন্যে একজন খাদেম নিয়োগ করেছেন। দেশ বিদেশের বহু পর্যটক দর্শনার্থী ও স্থাপত্য বিশারদরা এই মসজিদ পরিদর্শন করেছেন। সরে জমিনে গিয়ে মসজিদের রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বে নিয়োজিত খাদেম আব্দুস সামাদের সাথে কথা হলে তিনি জানান, এই সুরম্য মসজিদ স্থলে যাওয়ার জন্যে পাকা কোন রাস্তা নেই। পাকা রাস্তা থেকে মাত্র কয়েক শত গজ কাচা রাস্তা মসজিদটিকে দুরগম করে রেখেছে। সংশিষ্ট বিভাগ মসজিদটিতে যাওয়ার জন্যে প্রসস্ত পাকা রাস্তা নির্মান করলে পরিদর্শনে আসা দেশ বিদেশের ভ্রমন পিয়াসী মানুষের যেমন তৃষ্ণা মেটাবে তেমনি মুসলিম স্থাপত্য সর্ম্পকেনতুন প্রজন্মের মাঝে ধারনা যোগাবে।
 |
অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক গাজী শাহ বন্দেগী (রহঃ) এর মাজার শেরপুরে
অমুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে আলাহ তায়ালার বানী ও তাঁর পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামের দাওয়াত প্রচারের জন্য হযরত শাহ বন্দেগী (রঃ) আজীবন কঠোর সাধনা করে গেছেন। তিনি বগুড়া জেলায় বিশেষত শেরপুর থানায় ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর পুরো নাম হযরত সদরুদ্দিন বন্দেগী (রহঃ) তিনি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার কারনে শাহ বন্দেগী ‘‘গাজী‘‘ হয়েছিলেন। ইতিহাসবীদদের বর্ননা থেকে জানা যায়, রাজা বলাল সেন বাহিনীর সাথে যুদ্ধে হযরত শাহ্ তুর্কান শহীদ হয়েছেন এই সংবাদ পাওয়ার পর বাবা আদম শহীদ (রহঃ) শাহ্ বন্দেগী সহ কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে শেরপুরে আসেন। যুদ্ধে শহীদ হওয়া শাহ্ তুর্কান (রহঃ) এর দাফন সম্পুন্ন করে বাবা আদম শহীদ বলাল সেন বাহীনির সাথে যুদ্ধের প্রস্ত্ততি গ্রহণ করেন। কিন্ত ততক্ষনে তথ্য বিভ্রাটের কারণে হিন্দু রাজা বলাল সেন ও তার বাহীনি আত্মহত্যা করেন। ফলে বিনা যুদ্ধে বাবা আদম শহীদ শাহ্ বন্দেগী সহ মুসলিম বাহীনি জয়লাভ করে। যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবা আদম শহীদ সহ তার অন্যান্য সফর সঙ্গীদের নিয়ে জেলার আদম দীঘি থানায় চলে গেলেও হযরত গাজী শাহ্ বন্দেগী (রহঃ) শেরপুর উপজেলার খন্দকার টোলা গ্রামে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এবং সেখাই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি সহ তার দুই পুত্র এখানে সমাহিত আছেন। তার এই সমাধি স্থানকে ঘিরে বর্তমানে খন্দকারটোলায় গড়ে উঠেছে হযরত শাহ্ বন্দেগী (রহঃ) কওমী মাদ্রাসা ও কমপ্লেক্স। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াকু এই সৈনিক গাজী শাহ্ বন্দেগীর মাজার জিয়ারতেও প্রায় প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসে।
 |
হযরত শাহ তুর্কান (রহঃ) মাজার কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত শেরপুর শহীদিয়া কামিল মাদ্রাসা
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে হযরত শাহ তুর্কান (রহঃ) এদেশে আগমন করেন। বগুড়া জেলায় তিনি ইসলামের সুমহান বাণী অমুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচার করেছেন। বাংলার তদানিন্তন হিন্দু রাজা বলাল সেনের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি আত্মৎসর্গ করেন এই জন্যে তিনি ‘‘শহীদ‘‘ নামে অভিহিত হন। ইতিহাসবীদদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বাংলার শাসনকর্তা রাজা বলাল সেনের বাহিনীর নির্মম নির্যাতন আর অত্যাচারে জন সাধারন যখন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঠিক তখনি নির্যাতিত মুসলিম জনতার মুক্তির লক্ষ্যে ও ইসলাম প্রচারার্থে (১০৪৭খ্রিঃ) হযরত বাবা আদম শহীদ (রহঃ) তাঁর বিশ্বস্থ অনুচর ও শিষ্য হযরত শাহ তুকার্ন, হযরত শাহ বন্দেগী, শাহ জালাল সহ কয়েকজন সুফিকে সঙ্গে নিয়ে সান্তাহার থেকে ৫ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে আস্তানা পাতেন। ত্রয়দশ শতাব্দীতে বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানায় আগমন করেন। ওই সময়ে হযরত শাহ তুর্কান এই সিদ্য পুরুষ মুষ্টিমেয় অনুচর সঙ্গীকে নিয়ে বগুড়ার শেরপুর শহরের নিকটবর্তী কুসুম্বী ইউনিয়নের বাগড়া কলোনী নামক স্থান থেকে রাজা বলাল সেনের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তিনি আত্মৎসর্গ করেন। এই জন্যে তিনি ‘‘শহীদ‘‘ নামে অভিহিত হন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে স্থানে তার মস্তক দেহচুত্য হয়ে ভুমি স্বর্শ করে সেই স্থানটি ‘‘শির মোকাম‘‘ এবং যেখানে তাঁর শিরশূর্ন দেহচুত্য হয় তা ‘‘ধর মোকাম‘‘ নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে রাজা বলাল সেনের সাথে (১১৬০ -১১৭৮ খ্রিঃ) যুদ্ধে শাহ তুর্কান নিহত হলে তার শিরটি দেহ থেকে অর্ধমাইল দুরে নিপতিত হয়। বর্তমানে শেরপুর শহিদীয়া আলিয়ামাদ্রাসার এরিয়ায় শাহ তুর্কানের ‘‘শিরমোকাম‘‘ এবং উপজেলার ধর্মমোকাম গ্রামে ‘‘ধরমোকাম‘‘ নামে এই দুটি পৃথক পৃথক স্থানে তার দরগা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুটি স্থান পবিত্র বলে বিবেচিত। প্রতিদিনই প্রায় অসংখ্য মানুষ ইতিহাস খ্যাত এই বীরশ্রেষ্ট শহীদ শাহ তুর্কান (রহঃ) দরগাঁহ শরীফে তাঁর মাজার জিয়ারত করতে ছুটে আসেন।
 |
শেরপুরে শহীদদের গণকবর
‘শহীদদের আত্মত্যাগের ঘটনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বগুড়ার শেরপুরে আজও তেমন কোন উলেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। শহীদদের গণকবরগুলো এখনো অযত্ন অবহেলায় পড়ে রয়েছে। অনেক গণকবর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার অনেকগুলোর অস্তিত্ব বিলীনের পথে। সরকারি বা বেসরকারি কোন সংস্থা স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারীদের শেষ চিহ্নটুকু ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। এ দীর্ঘ সময়ে উপজেলায় মাত্র একটি গণকবর সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তা প্রাচীর ও নামফলক স্থাপন করা হলেও বাকিগুলোর অবস্থা করুন।
সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শেরপুরের কল্যাণী, ঘোগা, দড়িমুকুন্দ ও বাগড়া কলোণীর গণহত্যার যে ঘটনা ঘটেছে তা বর্ণনা শুনে গাঁ শিউড়ে ওঠে।
পাক বাহিনী যুদ্ধকালীন সময়ে বাগড়া কলোনী গ্রামে নির্মম হত্যাযোজ্ঞ চালায়। স্বাধীনতাকামী এই গ্রামবাসীরা মিছিল নিয়ে রাস্তায় বের হলে তাদের ওপর নেমে আসে হায়েনাদের তান্ডব। শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ফরিদ উদ্দিন জানান, তার পিতা সদর আলী সরকারসহ গ্রামের প্রায় ২ শতাধিক লোক বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে মিছিল নিয়ে গ্রামের পাশের প্রধান সড়কে যান। এ দেশের স্বধীনতা বিরোধী চক্র এ খবর পাক সেনাদের কাছে পৌঁছে দেয়। কোন দিনের ঘটনা তা আজ তার মনে নেই। তখন দুপুর ১২টা। পাক সেনারা এসে মিছিল কারীদের ঘেরাও করে। পরে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় মনছের আলীর ইট ভাটায়। ভাটার ভিতর তাঁদের লাইন ধরে বসে রাখা হয়। এরপর শুরু হয় পাক সেনাদের বর্বরোচিত কায়দায় মানুষ হত্যা। প্রথমে বসে থাকা স্বাধীনতাকামী অসহায় মানুষদের ওপর বোমা বিষ্ফোরণ ঘটানো হয়। এরপর আহতদের ওপর চালানো হয় মেশিন গানের গুলি। যে ইটের ভাটায় রাত দিন লেলিহান শিখার উদগীরণ হত, সেই ভাটা নিমিষেই শহীদদের রক্তে সিক্ত হলো। তপ্ত ইটগুলোর দীর্ঘদিনের তৃষ্ণা যেন হায়েনারা মিটিয়ে দিল স্বধীনতাকামীদের রক্ত দিয়ে। এ ঘটনায় প্রায় ৫০/৬০ জন বাঙালী শহীদ হন। নির্মম এ ঘটনার পর উদ্ধার কারীরা দেখতে পান, আহতরা শহীদদের রক্ত চুষে খাচ্ছে। নিহতদের আত্মীয়রা নিজ নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে দাফন করায় এখানকার শহীদদের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তবে গ্রামের পূর্বপাশে একটি ভিটায় এক জায়গার ১০/১২ জনকে কবর দেয়া হয়েছে বলে গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন। এ স্থানটি বর্তমানে কয়েকটি তাল গাছ দিয়ে ঘেরা রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে সে দিনের ঘটনায় সকল শহীদদের নাম জানা যায়নি। ব্যাপক অনুসন্ধান করে এলাকাবাসী সূত্রে যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হচ্ছেন, আফসার মন্ডল, শরকত মন্ডল,আলী আকবর মন্ডল, আয়েজ উদ্দিন মন্ডল, আলতাব সেখ, সিফাত মোলা, কুদ্দুস,হোসেন, মনছের, খোকা, আফজাল, ঈমান, হযরত, সাত্তার, রিয়াজ উদ্দিন, যদিমুদ্দিন, সদর আলী সরকার, আজিজ ও নবা ফকির, সেদিন যারা নিহত হয়েছিলেন তারা
শহীদ আফসার মন্ডলের বিধবা স্ত্রী ফাতেমা (৬১) জানান, আমার স্বামীকে স্বধীনতার বছর মিলিটারীরা মেরে ফেলেছে। পুনর্বাসন তো দূরে থাক। র্দীঘ দিন পার হলেও আমাদের কেউ খোঁজ খবর নিতে আসেনি। এলাকাবাসী জানান, তারা গণকবরগুলো সংরক্ষনের জন্য উপজেলা পরিষদে আবেদন করলেও তা আজো বাস্তবায়ন হয়নি। কল্যানী এবং ঘোগার বদ্ধভূমির অবস্থাও একই। শুধু স্মৃতি হয়ে আছে। এ গণকবরগুলো পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায়। শহীদদের গণকবরগুলো সংস্কার বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকির হোসেন জানান, অতিসত্তর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে এসব গণকবরগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হবে।
 |
মা ভবানী মন্দির
উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ৫১টি পীঠস্থানের মধ্যে অন্যতম ঐতিহাসিক বগুড়ার শেরপুরের মা ভবানীর মন্দির। প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি ভারত, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও শ্রীলংকা থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে আসেন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এটি দেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থান এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।
বগুড়া জেলা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিন পশ্চিমে উপজেলারভবানীপুর গ্রামের সবুজ শ্যামলে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক লীলাভুমি মা ভবানী মন্দির। মন্দিরটির এক দিকে ভবানীপুর বাজার অন্য দিকে একটি উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত। আর মন্দিরের চারদিক ঘিরে ছোট বড় বেশ কয়েকটি পুকুর রয়েছে।
এই মাতৃমন্দির মহাশক্তির ৫১টি পীঠস্থানের অন্যতম। কালিকাপুরান অনুসারে দক্ষযজ্ঞে দেবী সতীর স্বামীনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। সতীর প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে নিয়ে দেবাদিদেব মহাদেব প্রলয় নৃত্য শুরু করেন। সেই মহাপ্রলয় নৃত্য থেকে বিশ্ব ব্রক্ষান্ড রক্ষা কল্পে স্বয়ম্ভু বিষ্ণু সুদর্শণ চক্র দ্বারা সতীর প্রানহীণ দেহ ৫১টি খন্ডে বিভক্ত করেন। সেই সব দেহখন্ড বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পতিত হলে একান্নাটি পীঠস্থানের উদ্ভব হয়। ভবানীপুরে দেবীর বামতল্প বা বামপাজরাস্থি মতান্তরে দক্ষিন চক্ষু পতিত হয়েছিল। এই পীঠস্থানে দেবীর নাম অর্পনা (ভবানী) এবং বামন ভৈরব। প্রাচীন এই মহাতীর্থক্ষেত্রের বর্তমান মন্দির অবকাঠামো নাটোরের মহীয়সী রানী ভবানী কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দী নিমির্ত হয়। জমিদার প্রথা উচ্ছেদের আগ পর্যন্ত নাটোরের ছোট তরফ এস্টেট এই মন্দিরের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করত। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর সরকার নাটোরের ছোট তরফ এস্টেট অধিগ্রহন করেন এবং দেবোত্তর এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য এ্যানুয়িটি নির্দারণ করেন। কিন্তু মন্দির অবকাঠামো সংস্কার ও পুনঃ নির্মাণ খাতে সরকারিভাবে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।
নাটোরের রানী ভবানী এস্টেট কর্তৃক দেবোত্তর ১২ বিঘা জমির ওপর ওই মন্দির অবকাঠামো স্থাপিত।প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির চত্বরের মধ্যে রয়েছে দক্ষিন মুখী মুল মন্দির, বামেশ ভৈরব শিবমন্দির, অপর তিনটি শিবমন্দির, ভোগ পাকশালা ৮০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৩২ ফুট প্রস্থ নাটমন্দির ( আটচালা) দুটি অতিথিশালা, বাসুদেব মন্দির, গোপাল মন্দির নরনারায়ন সেবাঙ্গন (শ্যামাপ্রসাদ সেবা অঙ্গন) শাঁখারী পুকুর, দুটি স্নান ঘাট, বেষ্টনী প্রাচীরের বাইরে তিনটি শিবমন্দির এবং একটি পঞ্চমুন্ড আসন রয়েছে।
নাটোরের রানী ভবানী ছোট তরফ এস্টেট এবং অন্যান্য জমিদারদের পক্ষ থেকে এই মন্দির অনুকুলে প্রচুর ভু-সম্পত্তি দান করা হয়। যা বিট্রিশ আমলের সিএস রেকর্ডভুক্ত রয়েছে। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৪ সালে জমিদার প্রথা উচ্ছেদের পর তৎকালীন সরকার ১৯৫৮ সালে শ্রী শ্রী ভবানীমাতা ঠাকুরাণী ও অন্যান্য মন্দিরের নামে ১৮৬ একর সম্পত্তি বরাদ্দ করেন। এই সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয় রাজশাহী বিভাগীয় রাজস্ব কর্মকর্তাকে। কিন্তু সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারন মন্দিরের নামে বরাদ্দকৃত দেবোত্তর ভু-সম্পত্তি পুকুর জলমহাল ইত্যাদি সবকিছুই ভুলবশত সরকার খাস খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে বলে মন্দির কমিটি সুত্রে জানা যায়। এ ব্যাপারে র্বতমান কমিটি রেকর্ড সংশোধনের জন্য আদালতে আবেদন করেছেন এবং বর্তমানে বিষয়টি বিচারাধীন আছে।
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র এই পীঠস্থান ও তীর্থক্ষেত্রে রামনবমী, শারদীয় দুর্গোৎসব, শ্যামা পুজা, মাঘী পুর্ণিমা, বাসন্তী দুর্গোৎসব, প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ওইসব অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি ভারত, নেপাল, ভুটানসহ অন্যান্য দেশ থেকেও প্রতি বছর হাজার হাজার পুন্যার্থী এই মন্দিরে সমবেত হন। মন্দির কমিটির অভিযোগ, নুন্যতম সুযোগ সুবিধা না থাকায় ১৯৮৮ সালে সম্পুর্ন বেসরকারি উদ্যোগে ভবানীপুর মন্দির সংস্কার উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। বিগত ১৪ বছরে এই কমিটি মন্দির চত্বরে বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে জনগনের দানকৃত অর্থের মাধ্যমে। মন্দির কমিটি নেতৃবৃন্দ জানান, ১৯৯৪ সালে তৎকালীন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী এই মন্দির পনিদর্শনে আসেন। এ সময় তিনি হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট থেকে সংস্কার কাজের জন্য ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। তারা আরো জানান, শেরপুর-ধুনট এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সালে ঘোগা বটতলা-ভবানীপুর রুটের ৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়। পরে তিনি একটি অতিথিশালা নির্মাণের জন্য আরো এক লাখ টাকা বরাদ্দ দেন। এছাড়াও মন্দিরের উন্নয়নকল্পে তিনি একাধিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন বলে তারা জানান।
পূজা অর্ঘদান বা ভোগদানঃ পুন্যার্থীদের পূজা অর্ঘদানের জন্য মন্দিরে ব্যবস্থা রয়েছে। মিষ্টান্ন ভোগের জন্য মন্দির চত্বরে মিষ্টির দোকান রয়েছে। এছাড়াও অন্ন ভোগ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্ন ভোগের সামগ্রী বেলা ১১টার মধ্যে কমিটি নিয়োজিত কেয়ারটেকারের কাছে জমা দিতে হয়।
বিরতিহীন বাসে বগুড়া শহর থেকে পনের ও অন্যান্য বাসে বারো টাকায় শেরপুর শহরে আসতে হবে। সময় লাগবে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট। এরপর শেরপুর উপজেলা সদর থেকে অটোটেম্পু, রিকসা, ভ্যানসহ অন্যান্য যানবাহন যোগেমা ভবানী মন্দিরে যাওয়া যায়। তবে মাত্র ১০ টাকা ভাড়ায় টেম্পুযোগে সরাসরি মন্দিরে যাওয়া যায়। এছাড়া ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ঘোগা বটতলা নেমে সেখান থেকেও রিক্সাভ্যানে মন্দিরে যাওয়া যায়।
সরকার বিভিন্ন সময় মন্দিরটির উন্নয়নের জন্য নানামুখী সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন করেছে। তারপরও দ্রুততার সাথে মন্দিরের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে আগের অবস্থায় ফিরে আনা এবং দর্শনার্থীদের সকল সুযোগ সুবিধা দিতে সরাসরি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। তবে এটি দেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থানের পাশাপাশি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS